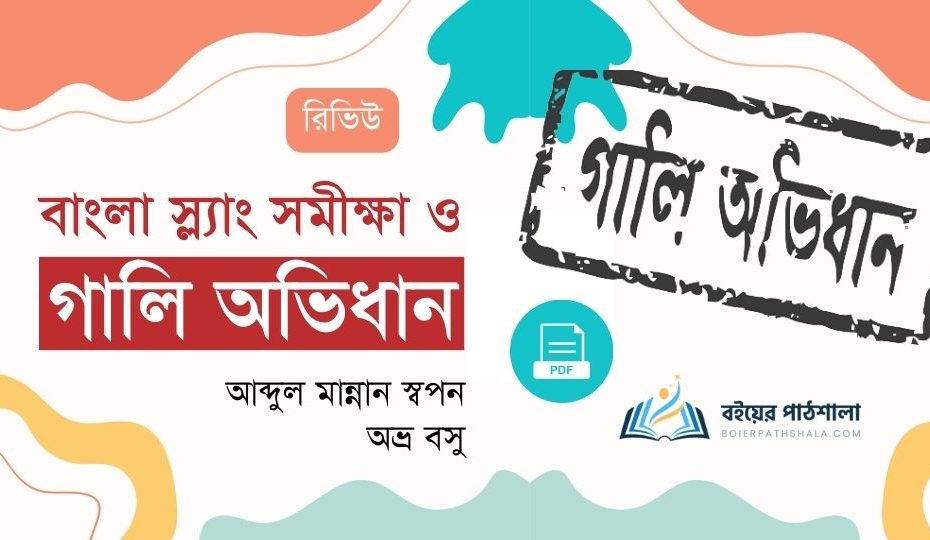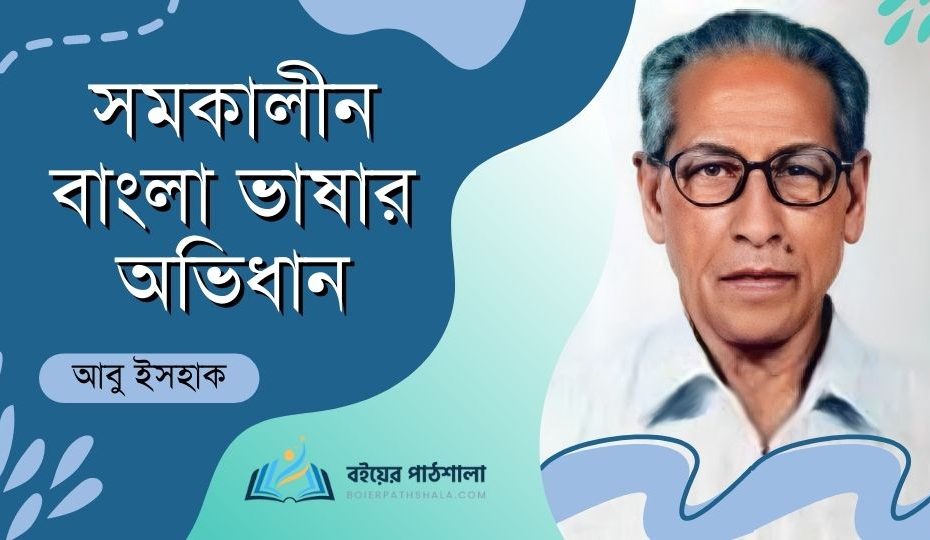যেকোন বইয়ের ফ্রি পিডিএফ পেতে অনুগ্রহ করে আমাদের PDF Download সেকশনটি ভিজিট করুন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বইয়ে সাজানো হচ্ছে আমাদের এই অনলাইন পাঠশালা। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।
তিনটা জিনিস মাতৃভাষায় বলার মত শান্তি আর নাই- গণনা, গান, এবং গালি। আজকে আমরা গালির চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়বো। গালাগালি কমবেশি সবাই করি। আপনার সেই দক্ষতাকে আরও শাণিত করবে এই দুটি বই। গবেষণালব্ধ এই বই দুটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই যে ধাক্কাটা খাবেন সেটা হলো এর উৎসর্গপত্র। দুজন লেখকই বইগুলো উৎসর্গ করেছেন উনাদের বাবা-মা কে। প্রথমেই এরকম উৎসর্গ দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠবে। এমন বই কেউ বাবা মাকে উৎসর্গ করে? এই বইটি তিনি কিভাবে তার বাবা মায়ের হাতে তুলে দিবেন? যাই হোক, পড়া শুরু করার পূর্বে বইগুলো সম্পর্কে লেখকদ্বয় ভূমিকায় কি লিখেছেন তা উনাদের মুখ থেকেই শোনে নিতে পারেন।
গালি নিয়ে লেখা এই “চমৎকার” বই দুটি পড়েন আর না পড়েন, অভ্র বসুর লেখা “বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান” বইয়ের ১০১ নাম্বার পেজে (পিডিএফ এর ৯৬ নাম্বার পেজে) চোখ বুলাতে ভুলবেন না। “চমৎকার” শব্দটি লিখতে গিয়ে হেসে খুন হচ্ছি আমি। এই শব্দটির অশ্লীল সমাস এবং ব্যাসবাক্য আপনাকে হাসাতে বাধ্য করবে। সেইসাথে বোনাস হিসেবে পাবেন আরও অসাধারণ কিছু সমাস। আপনাদের সুবিধার্থে দুটি বইয়ের পিডিএফ নিচে দেয়া হলো।
বাংলা গালির অর্থ থেকে ছন্দে ছন্দে গালি, কি নেই বইটিতে? ছেলেদের জন্য গালি, মেয়েদের জন্য গালি, গালি কত প্রকার ও কি কি, গালি কবিতা, খারাপ ভাষায় গালাগালি, চাইনিজ ভাষায় গালি, নোয়াখালী ভাষায় গালি , বাংলা গালি লিস্ট, ইতিহাস, হেডা গালির অর্থ কি, হ্যাডা মানে কি, বাইনচোদ মাদারচোদ মাদারি মাতারি মাদারির বাচ্চা শাউয়া হাউয়া স্যাটা গালির অর্থ কি ইত্যাদি সকল গালির মজার কিছু কালেকশন পাবেন এই বইয়ে।
আরও পড়ুনঃ সংস্কৃত নবরঙ্গ থেকে ইংরেজি Orange | কমলা | বাংলা ভাষার বিবর্তন
ভূমিকা
একটি ভাষার মানুষের মুখ নিঃসৃত শব্দই সে ভাষার শব্দসম্ভারের একটি অংশ। মানুষ প্রাত্যহিক কথনে যেমন স্বাভাবিকভাবে শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্য ব্যবহার করে তেমনি ক্রোধ-ক্ষোভে প্রতিপক্ষের উপর রাগ প্রকাশের জন্য শব্দকে বিকৃত করে ভিন্ন ধরনের শব্দ-বাক্য ব্যবহার করে থাকে। সে শব্দকে অশ্লীল শব্দ, ইতর শব্দ, গালি, বদকথা, বদবুলি, অকথ্যভাষা, জনবুলি, অপভাষা ইত্যাদি নানা অভিধায় ভাষাবিদগণ অভিহিত করেছেন। তবে শব্দগুলো বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। অর্থাৎ যে শব্দটি slang হিসাবে বেশি পরিচিত তার একটি যথার্থ প্রতিশব্দের আজও সন্ধান মেলেনি। এখানে লক্ষ্য করলে গালি শব্দটির সাথে অন্যান্য শব্দের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়।
গালি মূলত sense কেন্দ্রিক। গালিতে সব সময় অশ্লীল শব্দ নাও হতে পারে। একজন ক্ষুব্ধ মানুষ যখন ভাষার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে এবং বিপক্ষও ক্ষুব্ধ হয় তখনই সে ভাষা বা শব্দ গালি রূপে গণ্য হয়। গালি বা slang বিষয়ে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ভাষায় প্রচুর কাজ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর slang বা গালির পূর্ণাঙ্গ অভিধানও সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় গালি নিয়ে কোনো কাজ হয়নি।
ইংরেজি ভাষায় ষোড়শ শতক থেকেই slang সংকলিত হয়েছে। বাংলা ভাষার গালি বিষয়ে গত দুই দশক যাবৎ কলকাতায় কিছু গবেষণাধর্মী কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তা শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক গালির মান্য শব্দ নির্ভর। ‘ধমনি’ সাহিত্য পত্রিকার গালি সংখ্যা প্রকাশকালে গালি অভিধান করার আইডিয়া মাথায় আসে। ধমনির গালি সংখ্যায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার বাংলা ভাষাভাষীদের গালির শব্দ, কলকাতার বাংলা ভাষাভাষীদের গালির শব্দ, আসামের বাংলা ভাষাভাষীদের গালির শব্দ, ত্রিপুরার বাংলা ভাষাভাষীদের গালির শব্দ এবং বাংলাদেশের আদিবাসিদের ১১টি গোত্রের গালির শব্দ নিয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে সে প্রবন্ধগুলোতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু গালির শব্দ থাকে।
অভিধানের কাজ করতে গিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, যুবক, বৃদ্ধসহ নানা পেশাজীবী মানুষের কাছ থেকে গালির শব্দ সংগ্রহ করা হয়। এলাকাভিত্তিক গালির শব্দগুলোর বানান উচ্চারণ অনুযায়ী করা হয়েছে এবং গালির অনেক শীর্ষ শব্দ অভিধান বহির্ভূত হওয়ায় অর্থ নিজস্ব আইডিয়া থেকে করা হয়েছে। প্রতিটি এলাকার গালির শব্দের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট এলাকার উপভাষার বাক্যে দেখানো হয়েছে।
বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলাকে একটি ইউনিট ধরে বাংলাদেশকে ১৬টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি জেলার নামের আদ্যাক্ষর; কলকাতার নামের আদ্যাক্ষর এবং বাংলাদেশের ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নামের আদ্যাক্ষরের মাধ্যমে গালির শব্দটি কোন অঞ্চলে প্রচলিত তা দেখানো হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে বাংলাদেশের সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের গালির শব্দ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা থাকবে।
আসাম ও ত্রিপুরার গালির শব্দ পৃথকভাবে দেখানো গেল না প্রয়োগকৃত বাক্য দেখাতে না পারার কারণে। আশা করি পরের সংস্করণে আসাম ও ত্রিপুরার গালির শব্দ স্বাতন্ত্রিকভাবে দেখানো হবে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গালির ব্যবহার হয়েছে। অভিধানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গালির যে প্রয়োগ আছে তা দেখানো হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যেসব গ্রন্থে গালি ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট গালির শীর্ষ শব্দের সাথে দেখানো হয়েছে।
আরও পড়ুনঃ সিদ্ধান্তহীনতা দূর করার উপায় কি? আমরা কেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি?
সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত বাক্যগুলোর বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বানানরীতির ধারণা পাওয়া যাবে এবং বর্তমান বানানরীতির সাথে ভিন্নতা দেখা যাবে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গালির নতুন শব্দের জন্ম হয়। গালির শব্দ নিত্য যেমন সৃজিত হচ্ছে তেমনি অনেক শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের শব্দ বর্তমানেও ব্যবহৃত হচ্ছে আবার কিছু শব্দের ব্যবহার নেই। তাই অনেক শব্দের অস্তিত্বের ধারণা পাঠককে সন্দিহান করবে।
সংগৃহীত গালির শব্দগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণে বানান সংশোধন এবং প্রয়োগকৃত বাক্যের কাজটি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজ্ঞজন অত্যন্ত ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পাদন করেছেন। তাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া অভিধানের কাজটি করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কৃতজ্ঞতার তাদের নাম সর্বদা স্বীকৃত।
অভিধান সংকলনে দিকনির্দেশনা, সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তকের তথ্য প্রদান, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সরবরাহ এবং গালির শীর্ষ শব্দগুলো বর্ণানুক্রম অনুসারে বিন্যাসের নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে ঋণী করেছেন বাংলা একাডেমীর সহ-পরিচালক ড. এ. কে. এম. কুতুবউদ্দিন। কম্পোজের কাজটি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সম্পন্ন করে স্নেহের প্রদীপ চন্দ্ৰ দাস কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অপ্রকাশে আমার সাহিত্যকর্ম ও উৎসাহ-প্রেরণার কথা অব্যক্তই থেকে যাবে তিনি হলেন আমার গুরুপ্রতিম বাজিতপুর ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক এ. কে. মনজুরুল হক। তাঁর উপদেশ, পরামর্শ ব্যতিরেকে আমার লেখার জগৎ দেখার সুযোগই হতো না। অভিধানের প্রুফ সংশোধন ও পদবিন্যাসে সম্যক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সংকলনের কাজকে তিনি সহজ করে দিয়েছেন।
যেকোনো অভিধান সংকলন নিরন্তর পরিশ্রমলব্ধ কাজ। তিন বছর নিরলসভাবে অভিধানের কাজ করতে গিয়ে আমার পরিবারের অনেক কাজই উপেক্ষিত হয়েছে। পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় সাংসারিক কাজের দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে অভিধানের কাজটি করতে অপার সুযোগ করে দিয়েছেন আমার স্ত্রী ছালমা আক্তার কুমকুম। তাঁর এ ত্যাগস্বীকারকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে অবিচার করতে চাই না।
আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র নই। ভাষার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। অদম্য ইচ্ছায় অভিধান সংকলনের মনস্থ করি। ফলে ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে অভিধানে বহু ত্রুটি বা অসংগতি ধরা পড়া স্বাভাবিক। সর্বোপরি বাংলা ভাষায় গালি বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ অভিধান না থাকায় এতদ্সংক্রান্ত নমুনা নির্বাচনেও নিজস্ব ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। অধিকন্তু কোন অভিধানই সংস্করণ ব্যতীত পূর্ণতা পায় না। পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজ্ঞজন তথা পাঠকের উপদেশ ও পরামর্শের বিনীত প্রত্যাশা রইল।
—————-
আবদুল মান্নান স্বপন
বাজিতপুর
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
ভূমিকা
বাংলাভাষায় স্ল্যাং বিষয়ক গবেষণা বিশেষ হয়নি। স্ল্যাং সম্পর্কিত ধারণাও বাংলায় খুব স্পষ্ট নয়। সাধারণত স্ন্যাং বলতে অশ্লীল বা অশিষ্ট শব্দকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অশ্লীল বা অশিষ্ট শব্দ স্ল্যাং নিশ্চয়ই, কিন্তু তা স্ন্যাং-এর একটা অংশমাত্র। অশ্লীল স্ন্যাং ছাড়াও স্ন্যাং-এর বিচিত্র ধরনকে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেই কারণেই স্ন্যাং-এর সীমানা ইত্যাদি বিষয়কে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছি।
বাংলায় স্ল্যাং শব্দটির কোনো সন্তোষজনক পরিভাষা নেই। সে-বিষয়টিকেও আমরা আলাদা করে আলোচনা করেছি, এবং ‘স্ন্যাং’ শব্দটির প্রতিই আমাদের পক্ষপাতের কারণ স্পষ্ট করেছি। বাংলা স্ন্যাং বলতে ঠিক কী বুঝেছি, সেটা এই সূত্রে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কোনো ভাষায় স্ন্যাং-এর বিষয়টিকে দেখবার অনেক দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। প্রথমত, স্ন্যাং সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলাদা হয়ে যায়। শিক্ষিত শহুরে মানুষের স্ল্যাং এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের স্ন্যাং এক নয়; নারীপুরুষের স্ন্যাং আলাদা, বিভিন্ন উপভাষায় স্বতন্ত্র স্ন্যাং পাওয়া যাবে। সময়ের ভেদেও স্ন্যাং-এর চরিত্র বদলায়।
আমাদের গবেষণায় আমরা যে-ক্ষেত্রটিকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, সেটাকে এইভাবে নির্দেশ করতে পারি :
ক. সাধারণভাবে শিষ্টভাষীদের মধ্যে যে-স্ন্যাং ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই আমাদের লক্ষ্য।
খ. কলকাতা তথা নগরকেন্দ্রিক স্ল্যাংই আমাদের আলোচ্য।
গ. শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষের স্ল্যাং-ই আমাদের অন্বিষ্ট।
ঘ. স্ল্যাং-এর ঐতিহাসিক বিবর্তন নয় এককালীন প্রেক্ষাপটেই আমরা স্ল্যাং সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছি। অবশ্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটা ধরবার চেষ্টা একাধিক অধ্যায়ে সংক্ষেপে করা হয়েছে।
ঙ. উপভাষিক বা আঞ্চলিক স্ন্যাং, গ্রাম্য স্ন্যাং, পেশাগত স্ল্যাং ইত্যাদি আমাদের আলোচনার আওতার বাইরে থেকেছে, মান্য স্ল্যাং বা standard slang নিয়েই আমাদের গবেষণা। মান্য স্ন্যাং বলতে কী বুঝেছি, সেটাও আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে। অবশ্য আলোচনার সূত্রে মান্যেতর স্ন্যাং-ও আমাদের আলোচনায় কখনো কখনো এসেছে।
আরও পড়ুনঃ বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান সম্পাদক আবু ইসহাক
গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হয়ে স্ন্যাং-এর সীমানা নির্ধারণের কাজটি অত্যন্ত জটিল মনে হয়েছে। কোনো শব্দকে স্ন্যাং হিসেবে সনাক্ত করার ব্যাপারটি একেবারেই subjective। একই শব্দ কারো বিচারে স্ন্যাং, কারো বিচারে স্ন্যাং নয়। আমরা সাধারণভাবে যেখানে এ-জাতীয় দ্বন্দ্ব আছে, সেখানে সেই সমস্ত শব্দকে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত রেখেছি। ফলত অনেক বাগ্ধারা বা কথ্য শব্দকে ঠাই ওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্ন্যাং-এর পাশাপাশি আমরা সেই সমস্ত হেলিকেও রেখেছি, যাকে বলা যেতে পারে unconventional। পাশ্চাত্যের বহু স্ন্যাং-বিশারদই slang and colloquial wordsকে একসঙ্গে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, Eric Partridge-এর স্ন্যাং বিষয়ক বিখ্যাত অভিধানটির নাম হল A Dictionary of Slang and Unconventional English। বিষয়টিকে একটু বড়ো পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা সংগত। আমাদের গ্রন্থে আমরাও স্ন্যাং এবং unconventional language-এর আলোচনাই করেছি। আমাদের সংকলিত অভিধানটিতে বাগ্ধারা বা কথ্যশব্দকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছি।
শব্দসংগ্রহের কাজ মূলত দুটি উপায়ে করা হয়েছে। একটি লিখিত উপাদান, অন্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষানির্ভর মৌখিক উপাদান। বাংলা অভিধানসমূহ থেকে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য পেয়েছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, সংসদ বাংলা অভিধান প্রভৃতি অভিধানের কথা স্মরণীয়। বিশুদ্ধ স্ল্যাং বা তৎজাতীয় শব্দের অভিধান, যেমন কুমারেশ ঘোষ, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, সত্রাজিৎ গোস্বামী, মানসকুমার রায়চৌধুরী, সন্দীপ দত্ত প্রমুখের সংকলন আমাদের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। তবে এই সমস্ত সংকলন সর্বাংশে গ্রহণ করা হয়নি।
আমাদের কাজের আওতার কথা মাথায় রেখে ঝাড়াইবাছাই করেছি প্রয়োজনে। প্রবাদের একাধিক সংগ্রহও এই সূত্রে আমরা দেখেছি। সাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক স্ন্যাং আমাদের উপাদান জুগিয়েছে। বাংলা উপন্যাস, রম্যরচনা প্রভৃতি এবং উনিশ শতকের প্রহসন ও নকশা থেকে অনেক সময় শব্দ নিয়েছি। তবে সেগুলিকে মান্য স্ন্যাং বলা যাবে কিনা, সে-প্রশ্নটা সব সময়ই মনে রাখবার চেষ্টা করেছি। স্ন্যাং-এর মতো একটি বিষয়ের উপাদান বলা বাহুল্য, লোকমুখ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে।
আমাদের কাজ মূলত কলকাতাভিত্তিক। কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলিসহ (questionnaire) আলাপ আলোচনা করেছিল বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন, আড্ডার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একাধিক ছাত্রাবাসে গিয়ে আলোচনা করেছি এই উদ্দেশ্যে। পথেঘাটে চলতে কান খোলা রাখবার চেষ্টা করেছি, নতুন শব্দ কানে এলে জেনে নেবার চেষ্টা করেছি শব্দের প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। যদিও অপরাধজগতের ভাষা আমার আলোচনা আওতার বাইরে, তবু দক্ষিণ কলকাতার দু-একটি সমাজবিরোধী আড্ডায় যাবার সুযোগ ঘটে গেলে তা-ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি।
আরও পড়ুনঃ জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম-সনদ অথবা সার্টিফিকেটে নামের ভুল সংশোধন
বন্ধু-বান্ধব-শুভানুধ্যায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে নতুন শব্দ জানিয়ে গেছে, পরিচিতদের কাছ থেকে প্রশ্নাবলি পূরণ করে দিয়েছে অনেকে। স্ন্যাং নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধরনের কাজ বাংলায় সে-ভাবে হয়নি বলে কাজের পদ্ধতি নিজের মতো করে উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছে। ইংরেজিতে স্ন্যাং বিষয়ে অনেক আলোচনা থাকলেও সেগুলির মডেল বাংলায় কাজ করেনি। ভাষা সম্পর্কে অনুরাগের কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবার কথা ভেবেছি। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, স্ন্যাং বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় নয়। সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
নিজে সাহিত্যের ছাত্র বলে সাহিত্য বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনার কথা ভেবেছি, যদিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে অধ্যায়টির প্রতি সুবিচার করা গেল না বলে মনে বিস্তর অতৃপ্তি রয়ে গেল। ভবিষ্যতে, বাংলাসাহিত্যে স্ন্যাং বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছে রইল। এই গবেষণা কাজের জন্য সহায়তা পেয়েছি বহুজনের। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কারণ অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ পরোক্ষ, অন্যের মাধ্যমে সে-সমস্ত সাহায্য এসে পৌঁছেছে। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং নাম উল্লেখ না করতে পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করি।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করবার সিদ্ধান্ত আমার পিতা সোমেন্দ্রনাথ বসুকে স্মরণ করেই। আমার জীবনের চড়াই-উতরাই—কিছুরই সাক্ষী তিনি হতে পারলেন না আমার ছোটো ছেলেটার পড়াশোনা হবে না’—তাঁর এই সকৌতুক অভিমতই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর একমাত্র পর্যবেক্ষণ। ভাষা নিয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে আমার জীবনে তিনজনের ভূমিকা সর্বাধিক। আমার মা মঞ্জুলা বসুর কাছেই আমার ভাষাজিজ্ঞাসার সূত্রপাত। অর্থনীতির অধ্যাপিকা হলেও ব্যাকরণ, বিশেষত সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণে তাঁর অধিকার lay man-এর সীমা ছাড়িয়ে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তুলনীয়। আমার মধ্যে শব্দ নিয়ে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়েছিলেন আমার শুরু প্রয়াত অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দের ভাষাদর্শন আমাকে নানাভাবে আলোকিত করেছে।
আরও পড়ুনঃ হাট্টিমাটিম টিম ছড়াটির লেখক কে? সম্পূর্ণ কবিতার আসল রচয়িতা কে?
স্ল্যাং বিষয়ক নানাবিধ জিজ্ঞাসার তৎক্ষণাৎ উত্তরে আমাকে অভিভূত করেছেন বিশিষ্ট ইংরেজি স্ন্যাং বিশেষজ্ঞ Jonathan Green । ই-মেল-এর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঋদ্ধ হয়েছি। ভাষাতত্ত্বের নানাদিক সম্পর্কে Page 5 বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আমাকে সঞ্জীবিত করেছেন অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে অনেক সময় নতুন ভাবনা জেগেছে মনে, তার পরিচয় এই গ্রন্থে রইল। অধ্যাপিকা অলিভা দাক্ষীর সহায়তার কথা এইসূত্রে স্মরণ করি। অভিধান সংকলনের ব্যাপারে অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তবে তাঁর মতো একনিষ্ঠ ভাষাজিজ্ঞাসুর স্ন্যাং সম্পর্কে তীব্র রক্ষণশীলতা আমাকে বিস্মিত করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রয়াত অধ্যাপিকা শর্মিলা বসুদত্তের কথা এই প্রসঙ্গে বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আনুকূল্যে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে এই কাজটি শুরু করি। স্ল্যাং বিষয়টি গতানুগতিক নয়, নানাবিধ সামাজিক টাবু জড়িয়ে আছে বিষয়টি ঘিরে। এই রাম একটি বিষয়ে গবেষণার তত্ত্বাধায়ক হতে সম্মত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা রেখা মৈত্র। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা আর্থিীকে সতর্ক রেখেছে। নানা কারণে গবেষণার কাজ আগাগোড়া নির্মানতালে এগোয়নি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর সহযোগিতার ব্যত্যয় ঘটেনি। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ছিলেন এই গবেষণা নিবন্ধটির পরীক্ষক। তাঁদের লিখিত মতামত আমাকে কিছু কিছু অসংগতি সংশোধনে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক মজুমদার মৌখিক আলাপে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং গবেষণাটিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে অসংখ্য বইপত্র এবং পত্রিকা থেকে জেরা করে পাঠিয়েছিলেন আমার তৎকালে ‘প্রবাসী অগ্রজ’ অধ্যাপক অয়নেন্দ্রনাথ বসু। এদেশে সে-সমস্ত বইপত্র বা পত্রপত্রিকা সহজলভ্য নয়। বস্তুত, তাঁর সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা সম্ভবই ছিল না। বিশ্বভারতীতে আমার সহকর্মীরা অনেকেই গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর রেখেছেন, গবেষণাকর্ম দ্রুত শেষ করার এবং গ্রন্থপ্রকাশের জন্য তাগাদাও দিয়েছেন। এই সূত্রে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অধ্যপক রবিন পাল ও অধ্যাপক সুদীপ বসুর কথা বিশেষ করে স্মরণ করি।
আরও পড়ুনঃ পাশ মার্ক ৩৩ কেন ? ইতিহাস ও আমাদের ঔপনিবেশিক মনোভাব
গবেষণার বিষয়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রীরা। সংকলনের অধিকাংশ কৃতিত্বই তাদের। স্ন্যাং সংগ্রহের কাজ একার কাজ নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারো শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলি একত্র করতে তাঁদের প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। এইসূত্রে নানা সময়ে শব্দ, বা বইপত্র, বা বইপত্রের খোঁজ দিয়ে, বা অন্য কোনোভাবে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের নাম স্মরণ করি।
জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র পেয়েছি। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি থেকে। লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্তের উৎসাহ ও সহায়তা তাঁর উদার উপচিকীর্ষারই পরিচয় বহন করে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সোমেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থাগার থেকে নিরন্তর গ্রন্থ সরবরাহ করে কৃতার্থ করেছেন মীরা সেন।
আমার স্বাভাবিক ফাঁকিবাজির মধ্যেও সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে, এবং ফাঁকিবাজিতে প্রয়োজনীয় প্রশ্রয় জুগিয়েও যথোপযুক্ত তাগাদা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য অভিমুখীন করতে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু নিয়ত ব্যস্ত থেকেছেন, কিছু ত্যাগস্বীকারও করতে হয়েছে তাঁকে। প্যাপিরাসের কর্ণধার শ্রীঅরিজিৎ কুমার এই গ্রন্থটি ছাপতে সম্মত হয়ে তাঁর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়টির প্রতি তাঁর উচ্ছ্বাস আমার আনন্দের কারণ হয়েছে।
——
অভ্র বসু
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন।
১৬ জানুয়ারি, ২০০৫
আরও পড়ুনঃ যে বইগুলো জীবনে একবার হলেও পড়া উচিত | সেরা কিছু বইয়ের তালিকা
আরও পড়ুনঃ ভোকাবুলারি শেখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী ১০টি উপায়